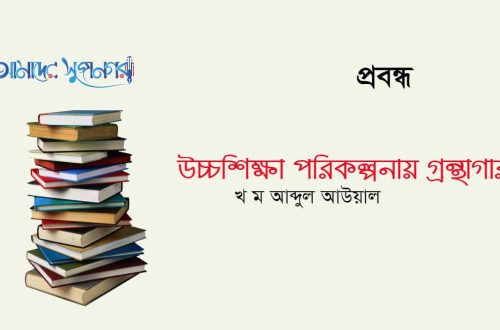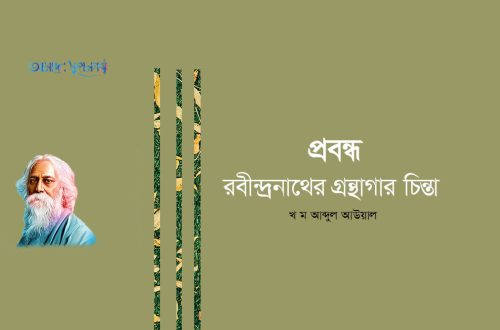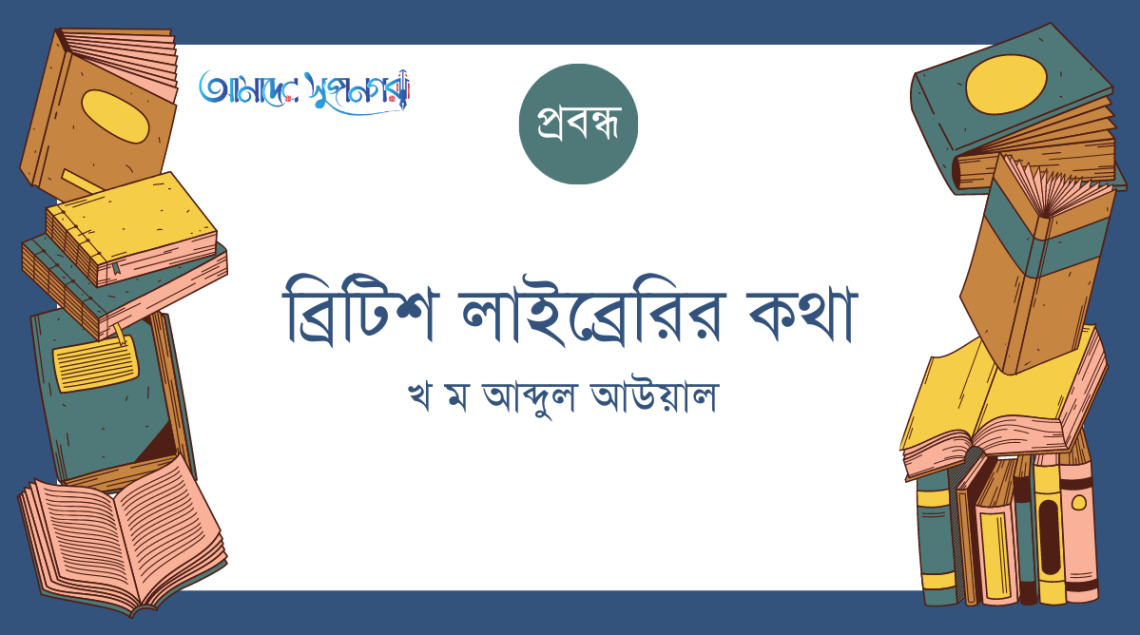
ব্রিটিশ লাইব্রেরির কথা
ব্রিটিশ লাইব্রেরির কথা
ব্রিটিশ কাউন্সিল ভিজিটরশিপে ইংল্যান্ডের কয়েকটি গ্রন্থাগার আমার দেখার সুযোগ হয়েছিল। ১৯৮৮ সালের এ ভিজিটরশিপের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্যায়ন ও তথ্য সরবরাহ প্রক্রিয়ায় গ্রন্থাগার ও প্রকাশনা কী ভাবে কাজ করে তা সরেজমিনে দেখা। এই কর্মসূচিতে যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়েছিল সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ‘দি এসোসিয়েশন অফ কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটিজ’, ‘কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট’, ‘ডিপার্টমেন্ট অব লাইব্রেরি, আর্কাইভ এন্ড ইনফরমেশন স্টাডিজ, ইউনিভার্সিটি কলেজ, লন্ডন, স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড এফ্রিকান স্টাডিজ, লন্ডন ইউনিভার্সিটি, ‘দি ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন স্টাডিজ, ইউনিভার্সিটি অব সাররে’, জর্জ এডওয়ার্ডস লাইব্রেরি, ইউনিভার্সিটি অব সাররে’, ‘দি ব্রিটিশ লাইব্রেরি, “ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি এ্যান্ড রেকর্ডস,’ ‘দি সিটি অব বার্মিংহাম সেন্ট্রাল লাইব্রেরি,’ ‘লাইব্রেরি এসোসিয়েশন, লন্ডন’ ও মিল্টন কিয়েন্সের ওপেন ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি। স্বল্প সময়ের পরিসরে শুধু পরিভ্রমণ ও পরিদর্শনের মাধ্যমে উন্নত বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সমন্বিত আধুনিক গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া সম্ভব নয়; তথাপি দেখার অভিজ্ঞতা অবহিত করলে অনেকে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন।
ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার:
ব্রিটেনের যে কোনো গ্রন্থাগার বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বলতে গেলে ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যে কথাটি বলতেই হয়, তাহলো সেখানে গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রগুলো ওতপ্রোতভাবে শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে জড়িয়ে আছে। এমন কি শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে সেখানে গ্রন্থাগার পরিকল্পনাই বেশী ব্যপ্তি লাভ করেছে। আসলে ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা মানে ব্রিটিশ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা ।
শিল্প ও বাণিজ্যের সাথে শিক্ষাকে এমন ভাবে সম্পৃক্ত করে শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, ব্রিটিশরা যেন শ্রেষ্ঠ বণিকজাত হিসেবেই আত্মপ্রকাশ ও প্রসার লাভ করতে পারে। এই লক্ষ্যে ব্রিটিশ জাতি রক্ষণশীল। ব্রিটিশ শিক্ষানীতি এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও যুগোপযোগী হওয়া সত্ত্বেও আদর্শে এবং প্রয়োগে অবশ্যই রক্ষণশীল। কিন্তু শিক্ষা প্রশাসন মোটেই কেন্দ্রীভূত নয়। প্রাকবিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের (Local Education Authority) দ্বারা পরিচালিত হয় এবং স্থানীয় সরকারের আদায়কৃত ট্যাক্স বা কর দিয়েই সকল খরচ নির্বাহ হয়ে থাকে। ব্রিটেনের সর্বত্রই শিক্ষার গুণগত মান সমুন্নত রেখে উন্নয়নের কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে।
ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার মূলকথা হলো ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত ও উন্নত করা, যাতে করে ব্যক্তি তার এবং সামগ্রিকভাবে সমাজ ও দেশের কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে। ব্রিটেনের শিক্ষা প্রশাসনের দায়িত্ব রয়েছে Secretary of State for education and science অর্থাৎ শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ওয়েলস, স্কটল্যান্ড এবং উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের সেক্রেটারি অব স্টেট ফর এডুকেশন অ্যান্ড সাইন্স সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই তাদের নিজ নিজ রাজ্যের সকল শিক্ষা পরিচালনা করে থাকেন, এমন কি বিশবিদ্যালয় শিক্ষা পর্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা যথার্থ অর্থে সার্বভৌম। কলেজ, পলিটেকনিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো স্বনিয়ন্ত্রিত, স্বাধীন ও সার্বভৌম।
ব্রিটিশ গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থাপনা:
ব্রিটেনের গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বৈচিত্র্যে এবং বৈভবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠদের মধ্যে অন্যতম। গবেষক, ব্যবসায়ী এবং জনসাধারণের জন্য পৃথিবীর প্রকাশিত জ্ঞান ও সংস্কৃতির অপরিসীম ভাণ্ডার রূপে গড়ে তলো হয়েছে ব্রিটেনের গ্রন্থাগারগুলো। এগুলো যেমন সংগ্রহে তেমনি সংরক্ষণ ও সঞ্চয়ে সমৃদ্ধত। বিশেষ করে গণ গ্রন্থাগারগুলো অবারিতদ্বার সার্বজনীন এবং সেনসরবিহীন। বর্তমানে সকল গ্রন্থাগারেই সর্বাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। বলা হয়ে থাকে যে লন্ডন হচ্ছে তথ্য সম্পদে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এর কারণ হচ্ছে সমবায় গ্রন্থাগার নেটওয়ার্ক (Co-operative library network), পেশাগত দক্ষতা এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা।
কি গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায়, কি তথ্য বিনিময় বা বিতরণ কার্যক্রমে ব্রিটেনই ডাটাবেজের পথিকৃৎ এবং বিপণনকারী। প্রতিবছর ব্রিটেনের প্রকাশকরা অন্যূন ৫০ হাজার নতুন বই প্রকাশ করে এবং তার অর্ধেক বইয়ের দ্বিতীয় মুদ্রণ ছাপায়; যা থেকে বার্ষিক আয় প্রায় ২০০ কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং তন্মধ্যে ৮০ কোটি পাউন্ড উপার্জিত হয় শুধু বই রপ্তানি করে।
বিলেতের লাইব্রেরিগুলোকে ন্যাশনাল লাইব্রেরি, একাডেমিক লাইব্রেরি, পাবলিক লাইব্রেরি এবং মিউজিয়াম ও স্পেশাল লাইব্রেরি এই পাঁচটি ভাগে বিন্যস্ত করা হলেও আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে গ্রন্থাগার সহযোগিতা (library co-operation) এত সুদৃঢ় এবং সচল যে, যে কেউ যে কোনো গ্রন্থাগার থেকে বিশ্বের তাবৎ জ্ঞান ভাণ্ডারকে চোখের পলকে নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে। উল্লেখ্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষা এবং এই পেশাজীবীদের সাংগঠিনক তৎপরতাও এ ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ছাড়াও রয়েছে গ্রন্থাগার বিষয়ে সরকারি অধ্যাদেশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সক্রিয় ভূমিকা । গ্রন্থাগারের জন্য রয়েছে পৃথক মন্ত্রণালয়। এর নাম হচ্ছে The Office of Arts and Libraries (OAL)। পূর্বে এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থাৎ The department of Education and Science এর অংশ ছিল।
আরও পড়ুন প্রবন্ধ গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার
১৯৬৪ সালের Public Library and Museums Act এর দ্বারা গ্রন্থাগারের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় করা হয়েছে। এই মন্ত্রণালয়ের একটি নীতি আছেযার আওতায় এমন সুদৃঢ় ও সুবিন্যস্তভাবে ব্রিটিশ গ্রন্থাগারগুলো গড়ে তোলা হয়েছে। সরাসরি অর্থ বরাদ্দ করা এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার জন্য এই মন্ত্রণালয়ে পেশাজীবীদের নিয়ে একটি Advisory Council আছে। এই মন্ত্রণালয়ের legal deposit বা আইন বলে সংগ্রহ নীতির দ্বারা প্রতিটি প্রকাশিত বই ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে সংগৃহীত হয়ে থাকে। আরও যে কয়েকটি অফিস বা দপ্তর ব্রিটিশ লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনাকে সহায়তা করে, সেগুলো হলো ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রেড এ্যান্ড ইন্ডাজট্রিজ এর Information Technology Asvisory Panel. এর কাজ হচ্ছে তথ্যের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব বের করে তার বিপণন করা। পাবলিক রেকর্ড অফিস এবং ডাটা প্রটেকশন এ্যাক্ট বিলেতের লাইব্রেরি সার্ভিসে উৎকর্ষতা যেমন বৃদ্ধি করেছে তেমনি ব্যবস্থাপনায় International Information Service ব্রিটিশ লাইব্রেরির অগ্রণী ভূমিকা নিতে সহায়তা করছে। ব্রিটিশ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং এর তথ্য বিনিময় কার্যক্রমই ব্রিটেনকে উন্নত বিশ্বের শ্রেষ্ঠদের মধ্যে টিকিয়ে রেখেছে।
ব্রিটিশ লাইব্রেরি:
আমাদের দেশের যাঁরা লন্ডনে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য যান, তাঁরা সবাই ব্রিটিশ লেন্ডিং লাইব্রেরির কথা জানেন। পৃথিবীর যে কোনো দেশের জ্ঞানান্বেষী মাত্রই ব্রিটিশ লেন্ডিং লাইব্রেরির সেবা ও কার্যক্রমের সাথে পরিচিত। বর্তমানে ব্রিটিশ লেন্ডিং লাইব্রেরি ব্রিটিশ লাইব্রেরির অংশ বিশেষ। বস্তুত ব্রিটিশ লাইব্রেরি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরিগুলোর একটি। ব্রিটিশ লাইব্রেরির নতুন ভবন নির্মিত হচ্ছে সেন্ট প্যানক্যাসে। সেন্ট প্যানক্যাস হচ্ছে লন্ডনের কেন্দ্রস্থলে ইউস্টোন নামক লন্ডনের বিখ্যাত স্টেশনের মুখে। ইউস্টোন থেকে ব্রিটিশ রেল প্রতি মুহূর্তে সমগ্র লন্ডন শহর তো বটেই দেশের দুরদূরান্তের সাথে এমন কি ইউরোপ মহাদেশের সাথে রেল যোগাযোগ স্থাপন করে সময় এবং দূরত্বের ব্যবধানকে ঘুচিয়ে দিয়েছে। যোগাযোগই যে উন্নয়নের চাবিকাঠি তা যেমন ব্যবহারিক জীবনের সর্বত্র বাস্তবায়ন করতে ব্রিটিশ জাতি সক্ষম হয়েছে তেমনি লাইব্রেরির ক্ষেত্রেও।
ব্রিটিশ লাইব্রেরি ব্রিটিশ জাতির জাতীয় গ্রন্থাগার। ১৯৭২ সালের জাতীয় সংসদে বিল পাস করে এই নতুন ব্রিটিশ লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৭২ সালের পার্লামেন্ট এ্যাক্টে যে ব্রিটিশ লাইব্রেরির সৃষ্টি করা হয়, তার আর্কিটেক্ট ছিলেন প্রফেসর সি এস জেউলসন। ভূগর্ভে চারতলা এবং ভূপৃষ্ঠে ৮ তলা বিশিষ্ট এই গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে মোট ৬৩৮ জন পাঠক একত্রে পড়াশুনা করার ব্যবস্থা রয়েছে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ এই গ্রন্থাগারে এ পর্যায়ে ৬৫০ জন কর্মচারী গ্রন্থাগার পরিচালনায় নিয়োজিত রয়েছে।
নতুন যে ব্রিটিশ লাইব্রেরি গঠন করা হয়েছে, তাতে ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি, ন্যাশনাল রেফারেন্স লাইব্রেরি, লাইব্রেরি অফ সাইন্স এ্যান্ড ইনভেনশন, ন্যাশনাল সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, ন্যাশনালা লেন্ডিং লাইব্রেরি ফর সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি, ব্রিটিশ ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফী এবং অফিস ফর সায়েন্টিফিক এ্যান্ড টেকনিক্যাল ইরফরমেশন (OST)- কে একীভূত করে গঠন করা হয়েছে। বৃটিশ লাইব্রেরিতে আরও দুটি লাইব্রেরি ইতোমধ্যে যুক্ত হয়েছে সে দুটি হচ্ছে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি এ্যান্ড রেকর্ডস এবং ন্যাশনাল সাউন্ড আর্কাইড। ব্রিটিশ লাইব্রেরি সরাসরি অফিস অফ আর্টস এ্যান্ড লাইব্রেরিজ নামক মন্ত্রণালয় থেকে বার্ষিক অনুদান পেয়ে থাকে।
আরও পড়ুন ভাষা নিয়ে ভাবনা
ব্রিটিশ লাইব্রেরি মূলত চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। যেমন:
১. Humanities and social science
২. Science, Technology and Industry
৩. Bibliographic services এবং
৪. Research and Development.।
১৯৮৮ সালে মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে ১,১২,৪৫,০০০ ভল্যুম বই পুস্তক ছিল। ১,২৬,০০০ ভল্যুম পাণ্ডুলিপি এবং প্রায় ৫০ হাজার সংবাদপত্র ছাড়াও আরও ছিল বিচিত্রধরণের বিপুল পরিমাণ ম্যাপ। মুদ্রিত সঙ্গীতস্ট্যাম্প এবং বিশ্বের বিচিত্র ধরণের রেকর্ডেড সাউন্ডও রয়েছে এই গ্রন্থাগারে।
বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং শিল্প বিভাগে দুই লক্ষ মনোগ্রাফ, ত্রিশ হাজার চলতি সাময়িকী এবং প্রায় ২৬ লক্ষ পেটেন্ট (যা Science Referecne and Information Service (SRIS) থেকে সংগৃহীত) রয়েছে। সকল তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে কম্পিউটারের অন লাইনে এবং Business Inforamtion Service এ লিখিত অথবা টেলিফোনে মৌখিকভাবে সরবরাহ করা হয়। ডক্যুমেন্ট সাপ্লাই সেন্টার থেকে সকল বিষয়ের ফটোকপি ও কাঙ্খিত বস্তু সরবরাহ করা হয়ে তাকে। বছরে তিন লক্ষেরও অধিক এই ধরণের তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে।
Bibliographic Services বিভাগ Copyright Receipt Office এর কাজ করে এবং British National Bibliography, British Catalogue of Music, British Education Index, Books in English 4 Serials in British Library ইত্যাদি রেফারেন্স বইগুলো প্রস্তুত করে তাকে। এগুলো আবার সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ কম্পিউটারে Machine Readable Catalogue (UK MARC) রূপান্তরিত করে রাখা হয়। যে কেউ on line access-এ বা British Library Automated Information Service- BLAISE-LINE এ উক্ত সকল তথ্য বা British Books in Print এর সকল তথ্য অবগত হতে পারেন।
Research and Development বিভাগে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের যাবতীয় গবেষণা পরিচালিত হয়ে থাকে। এই বিভাগ থেকে গবেষণা লব্ধ ফলাফল ভিত্তিক সেমিনার, সম্মেলন ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করে এবং প্রকাশনার মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া এবং বাস্তবায়ন করার জন্য অন্যান্য লাইব্রেরিকেও অনুদান দিয়ে সাহায্য করে থাকে।
ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি এ্যান্ড রেকর্ডস:
ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি এ্যান্ড রেকর্ডস একটি অসামান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এর বিপুল সংগ্রহরাজির মধ্যে রয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও ইন্ডিয়া অফিসের কার্যাবলীর সকল প্রকার দলিলাদি এবং ভারতবর্ষসহ সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া এবং এর প্রতিবেশী দেশসমূহ সেন্ট হেলেনা, দক্ষিণ আফ্রিকা, উপসাগরীয় দেশসমূহ, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, চীন এবং জাপানের সাহিত্য ও ইতিহাসের দলিল দস্তাবেজ। এই লাইব্রেরি গড়ে উঠেছে একটি সযত্নে সচেতন একক প্রয়াসের দ্বারা। ইংরেজদের একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি হিসেবে ১৬০০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রাজকীয় সনদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্ডিজের (Indis) এর সাথে ব্যবসা করার মূখ্য অধিকার এই কোম্পানিকে দেয়া হয়। কোম্পানীর রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য ১৭৭১ সালে একজন রেজিস্ট্রার ও একজন কিপার নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে ১৮০১ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী একটি লাইব্রেরি গড়ে তোলে। উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্যের বই পুথিপত্র ও পাণ্ডুলিপির যথাযথ সংগ্রহ গড়ে তোলা। ১৮৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়া অফিস নামক প্রতিষ্ঠানে কোম্পানীর রেকর্ড এবং লাইব্রেরিকে হস্তান্তর করা হয়।
১৯৪৭ সালে পাকভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতার পর কোম্পানীর এই রেকর্ড ও লাইব্রেরিকে প্রথমে কমনওয়েলথ রিলেশন অফিস পরে কমনওয়েলথ অফিস এবং তারপরে ফরেন এ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিসে হস্তান্তর করা হয়। ১৯৭১ সালে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি এবং ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডকে একত্রিত করে একটি অধিদপ্তরে আনা হয় এবং ইংল্যান্ডের হোয়াইট হল থেকে ব্লাক ফেয়ার্স রোডে একটি একক ভবনে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৮২ সালের এপ্রিল মাস থেকে ব্রিটিশ লাইব্রেরি বোর্ড এই অফিস ও লাইব্রেরি রেকর্ডসের সমগ্র সংগ্রহসহ প্রশাসনিক ও অন্যান্য দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এখন এটি ব্রিটিশ লাইব্রেরির অংশ বিশেষ। অবশ্য এর মালিকানাসত্ত্ব এখনও পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হাতে (Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs) রয়েছে।
আরও পড়ুন প্রবন্ধ গ্রন্থাগার আইন
একসময়ে যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেতো না, সেই পৃথিবীব্যাপী ঔপনিবেশিক শাসনামলেই এই ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির সংগ্রহ সমৃদ্ধতর হয়। ফলে সমুদয় সংগ্রহের বিপুল অংশ জুড়ে রয়েছে বৃটিশ শাসনামলের ভারতীয় ইতিহাস এবং আধুনিক দক্ষিণ এশিয়ার বিষয়াবলী। এগুলির মধ্যে এক লক্ষেরও অধিক বই ইউরোপীয় ভাষায়, আড়াই লক্ষেরও বেশী বই এশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় রচিত। সাত হাজারেরও বেশী সংবাদপত্রসহ বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ভাষার সাময়িক পত্র পত্রিকা রয়েছে। এগুলো এতই দুর্লভ এবং অনন্য যে এর সংগ্রহমূল্য আজ অসাধারণ। প্রাচ্য দেশীয় বই পুস্তকের মধ্যে বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত, প্রাকৃত, উর্দু, তামিল, তেলেগু, আরবি এবং ফার্সি ভাষায় রচিত বই পুস্তকই সর্বাধিক। এছাড়া ৮০টি আঞ্চলিক ভাষার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগ্রহ রয়েছে। এ দেশের হাতে লেখা প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সংখ্যা হচ্ছে ২৮ হাজার। পাণ্ডুলিপির মধ্যে সংস্কৃত, ফার্সি, আরবি ও তিব্বতী ভাষার পাণ্ডুলপি সমধিক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য বিষয়ক এবং ব্রিটিশ শাসনের নানা রকম রেকর্ড এবং দলিল দস্তাবেজ রয়েছে দুই লক্ষ।
এ ছাড়াও তৎকালীন সরকারি প্রকাশনা রয়েছে ৭০,০০০ এবং ৩৬,০০ মানচিত্র। এগুলোকে ভাগ করা হয়েছে এভাবে “ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৬০০১৮৫৮, বোর্ড অফ কন্ট্রোল ১৭৮৪ ১৮৫৮, ইন্ডিয়া অফিস ১৮৫৮১৯৪৭ এবং বামী অফিস ১৯৩৭ ১৯৪৮। প্রাইভেট পেপার নামে আর একটি বিভাগ রয়েছে। এখানে তৎকালীন ভারতবর্ষের ভাইসরয়, গভর্ণর, সিভিল সার্ভেন্ট এবং সামরিক কমকর্তাসহ ব্যবসায়ী পণ্ডিতবর্গ, ভ্রমণকারীদের ডাইরি ও অন্যান্য ব্যক্তিগত চিঠিপত্র লেখালেখির সংগ্রহ রয়েছে। বর্তমানে এগুলির ভল্যুম ১৫,০০০। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি এ্যান্ড রেকর্ডসের পৃথকভাবে শুধু বাংলা বইয়ের সংগ্রহ হচ্ছে ৩১,০০০। এগুলো ক্যাটালগ করা আছে। এই ক্যাটালগের নাম হচ্ছে ‘Catalogue of the Library of the India Office Vol – 2, Part 4: Bengali Oriya and Assamese books By I.E. Blumhandr (London 1905) এই ক্যাটালগে আরও কিছু বাংলা ডকুমেন্ট সংযোজন করে সমৃদ্ধ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আনিসুজ্জামান।
আরও পড়ুন ভালো মানুষ হওয়ার শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা
উল্লেখ্য যে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির এই বাংলা বিভাগে তখন যে মহিলা কর্মকর্তা কর্মরত ছিলেন, তার ঠাকুরদার বাড়ি ছিল বাংলাদেশের বরিশালে। তার সুবাদে কিছু দুর্লভ বই এখানে দেখার সুযোগ হয়েছিল। সেগুলো ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সেই ঔপনিবেশিক আমলে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এ বইগুলো ঢাকা, কলকাতা, বরিশাল থেকে সেই অসহযোগ আন্দোলন থেকে ভারত ছাড় আন্দোলনের সময়কালে রচিত ও প্রকাশিত বই। যেমন বিপ্লবী অবনী মুখার্জী,’ রাখালচন্দ্র ঘোষ, ঢাকা ১৯২৯ পৃ. ১৬৫, বরিশালের আনন্দ আশ্রম থেকে ১৯৩০ সালে প্রকাশিত; মুকুন্দ দাসের ‘কর্মক্ষেত্র’ নামক নাটক ইত্যাদি। কাজী নজরুল ইসলামের নিষিদ্ধ বইসহ ১০৭টি নিষিদ্ধ ঘোষিত বই ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে আছে। যে কোনো আগ্রহী পাঠক এবং পরিদর্শনকারী একটি রিডার্স টিকেটে সংগ্রহ করে এই লাইব্রেরিতে পড়াশুনা করতে পারে।
SOAS Library:
লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের School of Oriental & African Studies University of Lonon (SOAS) সোয়াসের প্রতিষ্ঠা ১৯১৬ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোয়াসকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করা হয় যাতে করে এখানে যে বিষয়গুলো পড়ানো হয় তা শুধু ব্রিটেনেই নয় গোটা বিশ্বে একক ও অন্যন্যসাধারণ। ১৯৬১ সালের হিতের রিপোর্ট অনুযায়ী, এই সোয়াসকে সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর জন্য অনন্য সাধারণ করে গড়ে তোলা হয়। এশিয়া ও আফ্রিকার সকল ভাষা এবং বিশেষ করে সমাজ বিজ্ঞানের সকল শাখায় উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা করার এক অনবদ্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সোয়াস এবং এ নিমিত্তে এর গ্রন্থাগার। রাসেল স্কোয়ারে লন্ডন মিউিজিয়ামের পাশে সুরম্য ভবনে শ্বেত পাথরে তৈরি সোয়াস এবং এর অভ্যন্তরে সেই বিশালাকার গ্রন্থাগার। মাথার উপরে কাঁচের তৈরি ছাঁদ ভেদ করে যেমন আকাশ দেখা যায়, তেমনি সর্বোচ্চ তলা থেকে একেবারে মাটির নীচের তলার পাঠক কক্ষও দৃশ্যমান।
গ্রন্থাগারের ডিজাইনটি এমনভাবে করা হয়েছে যেন এই গ্রন্থাগারের সকল সংগ্রহ যেন পাঠককে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এই বিশাল গ্রন্থাগারের সকল কোণায় জ্ঞানান্বেষীদের অনসন্ধিত বিচরণ। শ্রেণিকক্ষগুলো এমনভাবে বিন্যন্ত যে লাইব্রেরিকে এর অন্তর্ভুক্ত মনে হবে। এখানে শুধু বই ধার দেয়ার ব্যাপারটিতে অটোমেশন বা যান্ত্রিকীকরণ করা হয়েছে। শ্রেণিকরণ ও বই বিন্যাসের কৌশল পাঠককে আপনা আপনিই পথ দেখায় এবং অত্যন্ত সুক্ষ্ম চাহিদাটিও মেটাতে সক্ষম। ১২টি বিশেষ সেমিনার লাইব্রেরিতে এবং অঞ্চল বিশেষে অর্থাৎ এশিয়া থেকে আফ্রিকা এমনিভাবে গ্রন্থাগারকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। আবার এ ক্ষেত্রেও বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে অতি চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছে। প্রত্যেকটি শাখায় রয়েছে একজন করে সহকারি গ্রন্থাগারিক যেমন এশিয়া কক্ষ, এখানে যিনি আছেন তিনি এশিয়া বিষয়ে ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত, তিনি তাঁর এগারজন সহকর্মী নিয়ে শিক্ষার্থী শিক্ষক পণ্ডিত গবেষকদেরকে সেমিনার কক্ষে তাৎক্ষণিক সেবাসহ সহযোগিতা দিয়ে গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষকে একাকার করে ফেলেছেন। এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহে রয়েছে ছয় লক্ষ আইটেম।
আরও পড়ুন সমকালীন ভাবনা
অডিও ভিজুয়াল, ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরিসহ সেমিনার কক্ষগুলিতেও সার্বক্ষণিক সেবাদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও বিবিসির সঙ্গে তিনটি লাইনে সোয়াসের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়া বিভাগেই সোয়াস লাইব্রেরির প্রাচীনতম মূল। এই বিভাগের একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ বই হচ্ছে এই লাইব্রেরির ১ নম্বর একসেশন নাম্বারের বই। এই বিভাগের প্রায় সমুদয় সংগ্রহই হচ্ছে ভারতীয় উপমহাদেশের পুথিপত্র দ্বারা। পাণ্ডুলিপি, প্যাঙ্কলেট ও বই মিলিয়ে দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের সংগ্রহ ৫৯,০০০। এই গ্রন্থাগারের শ্রেণিকরণ ডিডিসির সঙ্গে বর্ণমালা যুক্ত করে ডিডিসিকে কিছুটা পরিবর্তিত করে নিজেদের উপযোগী করে করা হয়েছে।
ঘুরে আসুন আমাদের সুজানগর এর অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেইজে
ব্রিটিশ লাইব্রেরির কথা